Sharing is caring!
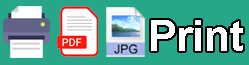
‘নারীর দৃষ্টিভঙ্গি বা নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে নয়, ইতিহাসকে উপন্যাসে তাঁরা পুনর্নির্মাণ করেছেন ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার উপলব্ধি দিয়ে। বলা যেতে পারে যে, ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা শিল্পের সত্য নির্মাণের ব্রত নিয়ে’— ডঃ ফারজানা সিদ্দিকা
আবেদীন কাদের
আমরা শীতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, তবে শীতের চেয়ে শীতের ভয়টা মনে হয় আমাকে একটু বেশি কাবু করে, তাই ঘরে সারাদিন টেবিলে বসে কাজ করতে গিয়ে একাধিক সোয়েটার গায়ে জড়িয়ে বসি। কিন্তু রান্নাঘরের গারবেজের ব্যাগ বাইরে রেখে আসতে গিয়ে টের পেলাম হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। বন্ধুরা যে আজ কীভাবে পৌঁছবেন আড্ডায়, তাই নিয়ে একটু শঙ্কিত ছিলাম। বিশেষ করে মাযহার, বদরুন ও অভীককে গিয়ে নিজে গাড়ি করে নিয়ে আসবো কিনা ভাবছিলাম।
এসব ভাবছি ঠিক সে-মুহূর্তেই দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম, দেখি মাযহার ঠিক এসে উপস্থিত হয়েছেন। সত্যিই ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়েছেন মাযহার, শীতের কাপড়ের আধিক্য দেখেই সেটা বুঝতে পারলাম। ওঁকে বসতে দিয়েই কফির আয়োজন করলাম, ঠাণ্ডাটা যদি কফিতে একটু সহনীয় হয়। এমন শীতে ভদকার সঙ্গে কমলার রস সত্যিই খুব কাজে দেয়, কিন্তু আড্ডার শুরুতেই হার্ড ড্রিঙ্কস খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, পুরো আড্ডাটা মাটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পানটাই মুখ্য হয়ে ওঠে।
তাই ভদকার ভাবনা বাদ দিয়ে কফি মাযহারের হাতে দিয়েই কথা শুরু করলাম। মাযহার আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডঃ ফারজানা সিদ্দিকার যে অভিসন্দর্ভটি পড়তে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটি এসেই টেবিলে রেখেছিলেন, আবার হাতে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। আজ ফারজানার দুটি বই নিয়ে আমাদের কিছুটা কথাবার্তা বলার কথা, যদিও আমি চাই আড্ডার কেউ বই দুটো নিয়ে লিখুন। তবে কাকে যে লিখতে অনুরোধ করবো তাই ভাবছিলাম।
মাযহারের ‘বইয়ের জগৎ’ বেঁচে থাকলে সেই পত্রিকার জন্য কাউকে না কাউকে দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বই দুটি নিয়ে গ্রন্থালোচনা হয়তো সহজতর হতো। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে আজকাল পরিশ্রম করে বই পড়ে লেখার মানুষও কমে যাচ্ছে। যাহোক তবুও ভাবলাম আমাদের নিজেদের পড়ার পর ভাবনাগুলো বিনিময় করতে পারি আড্ডায়। সেভাবেই মাযহারের হাতে ফারজানার অভিসন্দর্ভটি বই আকারে যা প্রকাশিত তা তুলে দিয়েছিলাম। মাযহার আড্ডার শুরুতেই বইটি নিয়ে কিছু কথা বললেন। আসলে নসরত আজ আসেন নি, তাই ভাবছি নসরতকে আগামী সপ্তাহের আড্ডায় তাঁর এবই নিয়ে আলোচনাটা না হয় করতে বলবো।
আমি নিজে যা ভাবি তা তেমন করে বলতে পারি না, তবে হয়তো কিছুটা লিখতে চেষ্টা করবো। মাযহার দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কথাসাহিত্যে যেভাবে এসেছে তা কিছুটা শুরুতে আলোচনা করলেন। কিন্তু নারী কথাশিল্পীদের সৃজনী শক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে গত প্রায় এক শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে নারীদের যেভাবে কিছুটা অবজ্ঞা করা হয়েছে তা বললেন। এবিষয়ে বলতে গিয়ে রাবেয়া খাটুনের উদাহরণ তুলে তিনি যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন নারী লেখকদের মূল্যায়ন করায় আমাদের দুই বাংলাতেই এক ধরণের পেট্রিয়ারকিক ‘প্রতাপ’ লক্ষ করা যায় সে-বিষয়ে জানালেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণত কোন লেখকের লেখার শিল্পমূল্য নিয়ে বলতে চাইতেন না, কিন্তু রাবেয়া খাতুনের সততা এবং মমতাময় হৃদয়ের জিজ্ঞাসাকে ঠেলতেও পারেন নি, তাই তিনি বিষয়টি নিয়ে নিজের কিছু পর্যবেক্ষণ যে জানিয়েছেন লিখিত আকারে তা শোনালেন।
এবিষয়ে ও বাংলাদেশের কবি ও কথাশিল্পীদের বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচনা, মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ আমি সত্তর দশক থেকে ঢাকা, কলকাতা ও নিউ ইয়র্কে বহুবার শুনেছি, তাই আমি মোটামুটি কিছুটা আন্দাজ করতে পারি তাঁর মতামত। যদিও আমি রাবেয়া খাতুনের প্রশ্নের জবাবে তিনি কী ভেবেছিলেন বা লিখেছিলেন তা আগে জানতাম না।
মাযহার শুরু করলেন ‘৪৭ সালের দেশভাগ আমাদের সাহিত্যে যেভাবে এসেছে তার কিছুটা বয়ান দিয়ে। কিন্তু ওঁর আলোচনার গুরুত্ব পেলো ডঃ সিদ্দিকার লেখার বা গবেষণার সৃষ্টিশীল দিকটি। এবিষয়ে বলতে গিয়ে মাযহার পরিষ্কার যে মন্তব্য করলেন সেটি হলো ফারজানা সিদ্দিকা সাহিত্যের মাঝে লুকিয়ে থাকা ‘ইতিহাসের’ অজানা প্রদেশের খোঁড়াখুঁড়ি কীভাবে করতে হয় এবং কথাশিল্পীর চোখে ‘ইতিহাস’ কীভাবে পুনর্নির্মিত আকারে ধরা দেয় সে-বিষয়ে ফারজানার অসাধারণ দৃষ্টি আমাদের কোন অনুধাবনে উপস্থিত করে!
ফারজানা এখানে সমাজবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে শিল্পের বিচার করতে গিয়ে কেন শিল্পকে সাধারণ চোখের বাইরে দেখেন, সেখানে শিল্পের বিচারে ঝুঁকির মাঝে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কী করে, তা কেমন করে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেন না, ভুলে থাকেন না শিল্পমূল্যকে তা নিয়ে বেশ কিছুটা আলোচনা করলেন মাযহার। আমি পুরো আলোচনাটাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে নীরবে শুনছিলাম। আমার নিজের এবিষয়ে লেখার ইচ্ছে আছে। আমি এই আড্ডার আলোচনায় শুধু প্রবন্ধের বই ‘নারীর সৃষ্টি নারীর দ্বন্দ্ব’ বইটির দুয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে কথা বলবো, তাই মাযহারের আলোচনার মাঝে কোন তক্কাতক্কিতে গেলাম না।
তাছাড়া মাযহারের কথাগুলো আমার ভাবনার কাছাকাছি। কিন্তু মাযহারের বইটি নিয়ে আলোচনা শুনতে শুনতে বার বার আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে পড়ছিলো যা ফারজানা তাঁর অভিসন্দর্ভের মুখবন্ধে খুব সাধারণভাবেই বলেছেন। কথাটি আটপৌরে মনে হলেও এটা একেবারেই সাধারণ কথা নয়। সম্প্রতি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা বা বিশেষ করে জেন্ডার স্টাডিজের পণ্ডিতরা একেবারে বায়-সাইন্সের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যৌথ গবেষণার ফলে এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে নারীদের দৃষ্টি তথা অনুভূতি পুরুষদের ‘প্রতাপ-সর্বস্ব’ অনুভূতির চেয়ে আলাদা। ডঃ সিদ্দিকা উল্লেখ করেছেন যে ‘আমি বিশ্বাস করি, নারীর সহজাত দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস পর্যবেক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।
নারীর সঙ্গে সমাজের উপরিতলের সম্পর্কই কেবল থাকে না, থাকে গভীরতলেরও। দেশভাগ প্রসঙ্গে বলা যায়, যখন কোন পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে তখন পরিবারটির পুরুষ সদস্য কেবল জমিজমা, ঘরবাড়ির শোকে মুহ্যমান থেকেছে, কিন্তু নারী থেকেছে আরও বেশি কিছুর জন্য। মাটি-লেপা উনুনের সঙ্গে, উঠোনের পাশে লাগানো লাউ গাছটার সঙ্গে, পুকুরে ভাসা কলমি আর পারের জবা ফুলের সঙ্গে নারীর থাকে প্রতিদিনের নিবিড় কোমল গোপন সম্পর্ক।
সেইসমস্ত সম্পর্কের গভীরতা কেবল নারীই বুঝতে পারে। অন্য কেউ নয়।’ সামান্য এই কটি কথার মধ্য দিয়ে ডঃ সিদ্দিকা সমগ্র নারী জাতির হৃদয়ের গভীর সংবেদনশীল দিকটির দিকে আলো প্রক্ষেপন করেছেন একজন শিল্প-গবেষক হিশেবে। আমি মাযহারকে কথা কটি স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েও নীরব রইলাম মাযহারের ভিন্ন একটি দার্শনিক ও শৈল্পিক বিষয়ের অবতারণা করার কারণে। আমি বরং সেই দিকটিই বেশি বোঝার চেষ্টা করলাম।
মাযহার খুব জোর দিয়ে একটি বিষয় উল্লেখ করলেন সেটি হলো কথাশিল্পীরা কীভাবে ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করেন, এর পদ্ধতি কী বা এর শৈল্পিক আবশ্যকতাই বা কী! সম্ভবত ডঃ সিদ্দিকা তাঁর গবেষণা এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণেও সে-বিষয়টির দিকেই বিশেষ অভিনিবেশ দিতে চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী যে-আলোতে ইতিহাসকে দেখেন, কথাশিল্পী বা বলা যায় যে কোন শিল্পীই ইতিহাসকে দেখেন ভিন্ন আলোকে!
এই ‘ভিন্ন দেখায়’ কোন দার্শনিক বোধ বা সাহিত্যিক ভাবনা কাজ করে কিনা! কথাশিল্পীরও তো ইতিহাসবিদ বা সমাজবিজ্ঞানীর মতো নিজস্ব জ্ঞান-ভূখণ্ডের ভাবনা আছে যা অন্য ডিসিপ্লিনকে ওভারলেপ না করেই চলতে পারে, বা ‘সৃজনে’ আদর্শ বা ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। বিষয়গুলো নিয়ে তাত্ত্বিকভাবে যতো গভীরভাবে ভাবা যায় ততো বেশি তা জটিলাকার ধারণ করে। যদি আলোচনার বিষয়টিকে সাহিত্যের আদর্শ বা ‘শিল্পের আদর্শ’ হিশেবে বা সাহিত্যের অন্তর্গত ‘দর্শনের’ ছায়া হিশেবে ভাবা যায়, যেমনটা সমাজবিজ্ঞানী কার্ল জুং চিন্তার পদ্ধতি হিশেবে দেখিয়েছেন।
চিন্তা যখন এক প্রবহমান-প্রসিডিউর, তখন তাঁর মাঝে জুং ‘Constructive’ পদ্ধতি-ভাবনা ও এর বিপরীতে ‘Reductive’ পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে জুং বিষয় বা দর্শনের ‘চারিত্র’ যেমন বুঝিয়েছেন, তেমনি শিল্পী বা কথাশিল্পী তাঁর ভাবনা বা শিল্পের বিষয়কে নিজস্ব ‘চারিত্র’ দান করে থাকেন তাঁর সৃষ্টিকলার মাধ্যমে, নিজের অজান্তেই। এ কারণে কথাশিল্পী তাঁর ‘ইতিহাস’ নির্মাণে ইতিহাসবিদের ‘নির্মাণ’ থেকে দূরে থাকেন আবশ্যিকভাবে, কিন্তু সেটাকেই ডঃ সিদ্দিকা ‘পুনর্নির্মাণ’ আখ্যায়িত করেছেন কিনা! নাকি শিল্পীর ইতিহাসবোধ আর ইতিহাসবিদের ইতিহাসবোধ সম্পূর্ণ আলাদা!
এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব আসলে ইতিহাস ‘পুনর্নির্মাণ’ কথাশিল্পী কীভাবে করেন বা আদৌ করেন কিনা। একজন ইতিহাসবিদ বিভিন্ন হিস্ট্রিওগ্রাফির ভিত্তিতে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে পারেন, ইতিহাসের উপাত্তকে খোঁজার পদ্ধতি একাধিক রয়েছে, এই পদ্ধতি বা মেথড উপাত্তের ভিন্নতা সৃষ্টি করে, তাই ইতিহাসবিদ শুধু কথাশিল্পীর থেকে আলাদা ইতিহাস সৃষ্টি করেন না, একজন ইতিহাসবিদ অন্য ইতিহাসবিদও থেকে আলাদা ইতিহাস সৃষ্টি করেন একই সময়ের বা একই শাসনকালের।
মোটা দাগে উদাহরণ দেয়া যায় ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখার প্রকল্প বিষয়ে। একজন অমলেশ ত্রিপাঠীর দেখা সময় একজন পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা রণজিৎ গুহর ‘দেখা’ থেকে একেবারে আলাদা। আবার একটু এগিয়ে গিয়ে আরেকজন তপন রায়চৌধুরীর দেখা বা লেখা থেকে আলাদা, যেমনটা আলাদা বিপান চন্দ্র বা রমিলা থাপারের লেখা। এর একাধিক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু গবেষণার পদ্ধতি যেমন আলাদা, উপাত্ত সংগ্রহের পথ ও বিশ্লেষণের ধরণও আলাদা। কিন্তু এটা তো গেলো উপাত্ত বা মেথডোলজি বিষয়ে পার্থক্য, এমনকি একেকজন ইতিহাসবিদ একেক রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হন একই উপাত্ত থেকে, এমনটাও দেখা যায়। তাছাড়া উপাত্ত বিশ্লেষণের পদ্ধতি আলাদা হলে ইতিহাসের ‘সত্য’ আলাদা হতে বাধ্য।
ঠিক এই কথার মধ্য দিয়েই আমরা অভিসন্দর্ভটি নিয়ে আলোচনার আরেকটি জটিল ডোমেইন বা সীমানায় পৌঁছলাম। সেটা হলো ‘ইতিহাসের সত্য’ এবং ‘শিল্পের সত্য’ তো কখনই এক রকম সত্য নয়। তাহলে এখানে ডঃ সিদ্দিকার অন্বেষণ কথাশিল্পীর ‘ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ’ নাকি ইতিহাসের ভিন্ন ‘সত্যের’ দিকে নির্দেশ করা। মাযহার তাঁর আলোচনার শুরুতেই ডঃ সিদ্দিকার অভিসন্দর্ভের অসাধারণ একটি অধ্যায় লিটারেচার রিভু, তার ব্যাখ্যা করে শিল্পের কোন চারিত্র বা ইতিহাসের কোন চারিত্রকে গভীরভাবে মূল্য দেন, সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। অর্থাৎ ডঃ সিদ্দিকার কাছে আসলে ইতিহাস ও শিল্পের অন্তর্বর্তী সীমান্তরেখা বা বিভাজন রেখা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তাও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। এই প্রথম অধ্যায় (১.১)‘বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠাকাল’, এই অধ্যায়ে লেখক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন উপনিবেশিক কালে বাংলা উপন্যাস কীভাবে লেখা হয়েছে।
সেদিক থেকে এই অধ্যায়টি অবশ্যই লিটারেচার রিভু বা অভিসন্দর্ভের নিয়মানুযায়ী যা লিখতে হয় সেরকম। অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসের জন্ম ইতিহাস এবং প্যাঁরিচাদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ থেকে পরবর্তী সকল গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস বিষয়ে মূল্যায়ন লেখক করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ডঃ সিদ্দিকা এখানে পরিষ্কার জানান যে প্যাঁরীচাদ মিত্রর লেখা ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাস হয়ে ওঠার সকল শর্ত হয়তো মেনে লেখা নয়। সেদিক থেকে তিনি মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’ অনেক বেশি উপন্যাসের কলা মেনে চলা লেখা। কিন্তু এই উপন্যাসের পটভূমি বাংলা অঞ্চল নয়, বরং রাজস্থান। এবং এর আদলটি ডঃ সিদ্দিকা মনে করেন ইউরোপ থেকে ধার করা। কিন্তু এবিষয়ে আলোচনায় ডঃ সিদ্দিকা উল্লেখ করতে ভোলেন নি যে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো একজন ইংরেজ নারী হানা ক্যাথেরিন মালেন্সের হাত ধরে প্রকাশিত হয় ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ, যা ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয়।
কিন্তু ডঃ সিদ্দিকা সঙ্গে সঙ্গে জানান যে এটি উপন্যাস হিশেবে বিবেচিত হবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যাহোক প্রথম অধ্যায় নিয়ে মাযহার কিছু বিহঙ্গদৃষ্টির কথা বলেই দ্বিতীয় অধ্যায় ‘সাহিত্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ’ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। আমি প্রথম অধ্যায়টি খুব মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করার পক্ষপাতি গ্রন্থালোচনা লেখা হলে, কারণ এই অধ্যায়টিতে শুধু উনবিংশ শতাব্দীর ছাপাখানার ইতিহাস বা ফোরট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০ সালে) প্রতিষ্ঠাই নয়, বরং বাংলার তথা ভারতের শিক্ষা জগতের সূচনালগ্নের ইতিহাস বিধৃত। মাযহার দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা শুরুর সময় আমি ভাবছিলাম প্রথম অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য বিষয়ে। তার মধ্যে অন্যতম হলো আমাদের সবার তরুণ বয়সে পড়া ই.এম ফরসটারের লেখা Aspects of the Novel গ্রন্থের সংজ্ঞানুযায়ী উপন্যাস বা গল্প কী সে-বিষয়ে পাঠককে সচেতন করা।
কিন্তু ডঃ সিদ্দিকা এই আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মত রেখেছেন, তাহলো ফরসটার কথিত ‘সাতটি বিষয়কে একত্রিত করেও কিন্তু কোন একক স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না, এর কোনটি দিয়ে উপন্যাস হতে পারে আবার কোনটি দিয়ে নয়।’ এছাড়া লেখক আরও মন্তব্য করেছেন, ‘তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস যেটি বাংলা সাহিত্যেরও প্রথম সার্থক উপন্যাস সেই ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে কিন্তু ফরসটারের নির্দিষ্ট সাতটি বিষয়ে বাংলার বিস্তৃত ভূমি, মানুষ, উপকথাকে পাওয়া যায়নি।’ একথা শেষ করেই লেখক সমকালীন একজন উপন্যাসিক ও সাহিত্য-তাত্ত্বিক দেবেশ রায়ের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। এসময়ে মাযহার একটু বিস্তৃত করে আলোচনা করলেন ডঃ সিদ্দিকার দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে, যেখানে শুরুতেই লেখক সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন ইতিহাস কী বা কাকে বলে ইতিহাস! তিনি লিখেছেন, ‘ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা-নিরপেক্ষ ভাগ থাকে। শাসক বদলের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে পালটে যায় ইতিহাসের পাঠ্যসূচি। ইতিহাস কার হাতে রচিত হয়েছে সেটিও একটি জটিল বিষয় হয়ে ওঠে। বিজয়ী আর বিজিতের লেখা ইতিহাসের গন্তব্য কোনদিনই এক হবার নয়।’
ডঃ সিদ্দিকার এই মন্তব্য কিছুটা ‘জোরালো’ Strong Comment হিশেবে বিবেচিত হতে পারে কারও কারও কাছে, আমরা ইতিহাস পড়েই তা শিখেছি, কিন্তু শিল্পীর হাতে লেখা ইতিহাস নিশ্চয়ই উপন্যাসিকের বা কথাশিল্পীর মনোজগতের ‘রাজনৈতিক বোধ’ বা ঝোঁকের প্রতিফলনকে এড়াতে কম দেখা যায়। তাই কথাশিল্পীকে সজাগ থাকতে হয় বিষয়টির অর্থাৎ ‘ইতিহাসের দর্শন’ তার কাছে কেমনভাবে ধরা দেয়, সে-বিষয়ে। এই বিষয়টা বেশ জটিল, একেবারেই সরলগতিতে চলে না, কারণ কথাশিল্পী বিষয়টা নিজের অন্তরে কীভাবে নিগোসিয়েট করেন বা সমাজমানসের সেই ছবিকে কীভাবে আঁকতে চান গল্পে বা উপন্যাসে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। আর এজায়গাতেই বড় পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ইতিহাসবিদের লেখা ইতিহাস ও কথাশিল্পীর আঁকা ‘ইতিহাসের’ মধ্যে। সুতরাং এটি ভীষণ জটিল এক অর্থে! এর ওপরই নির্ভর করে কথাশিল্পীর বা উপন্যাসিকের নিজের করা ‘ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ’!
মাযহার ডঃ সিদ্দিকার অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা করতে গিয়ে একাধিক বিষয় উঠে আসে আমাদের আড্ডায়, এর মধ্যে ইতিহাস ও কথাশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত বা এফিলিয়েটেড বেশ কিছু বিষয়। যেমন ইতিহাসের নিজস্ব দর্শন এবং কথাশিল্পের একান্ত শৈল্পিক সৌন্দর্যের দর্শন বা ‘নন্দনের’ দর্শন। এ দুটোর মধ্যেও পার্থক্য আছে মোটাদাগে। ডঃ সিদ্দিকার একটি বই ‘নারীর উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণঃ দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ’ নিয়ে কথা বলতে গিয়েই প্রায় ঘণ্টা তিনেক কেটে গেলো, এর মূল কারণ লিখিত অধ্যায় দুটি যে খুব সহজ বা সাধারণ সাহিত্যের বিষয় তা নয়, বরং কথাশিল্প এবং ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের এমন কিছু বিষয়ে লেখক তাঁর পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য দিয়েছেন যা আরও একাধিক ডিসিপ্লিনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের তক্কাতক্কিতে উৎসাহিত করে তুললো, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম হয় এই বই নিয়ে আমাদের পরের আড্ডায় বাকি অধ্যায়গুলো ধরে ধরে আলোচনা করতে হবে, নয়তো আমি বা মাযহার অথবা দুজনেই লিখিতভাবে ফর্মাল গ্রন্থালোচনা লিখে বই দুটি সম্পর্কে আমাদের মতামতগুলো জানাই।
কিন্তু আড্ডার শুরুতে আমার ইচ্ছা ছিলো মাযহারের আলোচনায় ডঃ সিদ্দিকার অভিসন্দর্ভের বিষয়ে যে বিশ্লেষণটা আমরা শুনি, এরপর তাঁর দ্বিতীয় বই ‘নারীর সৃষ্টি নারীর দ্বন্দ্ব’ বইটি নিয়ে আমি সামান্য দুয়েকটি কথা বলবো। এই বইটি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আমার বিশেষ করে বলার ইচ্ছা ছিলো কথাশিল্পী আশাপূর্ণা দেবী সম্পর্কে, বইয়ের একটি প্রবন্ধ ডঃ সিদ্দিকা লিখেছেন এই মহান কথাশিল্পীকে নিয়ে। আমার ভীষণ প্রিয় লেখক তিনি।
আমরা বাংলা সাহিত্যের বড় কথাশিল্পীদের মাঝে যে দুচারজন মহৎ লেখককে একেবারেই যে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দেই নি, তাঁদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন আমার মতে আশাপূর্ণা দেবী। আমি তাঁর লেখা সম্পর্কে দুচারটি কথা বলতে চেয়েছিলাম। আড্ডায় আরও কিছু বিষয় আলোচনার ছিলো, এছাড়া দুয়েকজন কবি ও কথাশিল্পীর লেখা পাঠেরও কথা ছিলো। আমার খুব প্রিয় কথাশিল্পী এসময়ের লেখক স্বপন বিশ্বাস। তাঁর গল্প ও কবিতা আমার প্রিয়, কিন্তু দেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর স্বপন আমাদের কয়েকটি রাজনৈতিক স্যাটায়ার কবিতা পড়ে শোনান, যা আমাদের খুব মুগ্ধ করেছিলো। স্বপন বিশ্বাসের অধিকাংশ গল্পের মধ্যে মুদ্রিত পঙক্তিগুলোর মাঝে শূন্য জায়গা জুড়ে থাকে অদৃশ্য এক গভীর রাজনৈতিক বীক্ষা, যা আজকের বাংলাদেশের কথাশিল্পে কম দেখা যায়। স্বপন সেটা বেশ মুনশিয়ানার সঙ্গেই করেন।
এছাড়া কবি এবিএম সালেহউদ্দীন পড়ে শোনান একাধিক খুব সুন্দর কবিতা। বেশ কিছুদিন আগে একটি কিশোর প্রেমের গল্প শুনিয়ে সালেহউদ্দীন আমাদেরকে মুগ্ধ করেছিলেন। সালেহউদ্দীনের পাঠের পর কবি শামস মমীন তাঁর সদ্য লেখা দুটি কবিতা পড়ে শোনান। আড্ডার একেবারে শেষ দিকে মাযহার ‘লেখকের বৈষয়িকতা’ শিরোনামের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পড়ে শোনান। এই প্রবন্ধটির শিরোনাম শুনে বা পড়ে পাঠকের ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে। ‘বৈষয়িকতা’ বলতে আমরা জাগতিক বিষয় আশয় বুঝে থাকি, কিন্তু মাযহার এই প্রবন্ধটিতে আসলে লেখক বা সমাজের সৃজনশীল মানুষদের দর্শনগত শৃঙ্খলার সঙ্গে আরও এমন কিছু বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন যা সাধারণত আমাদের সাহিত্যে আগে আমি কোন আলোচনা দেখি নি।
মাযহারের প্রবন্ধটি বিষয়ে আমার মনে অনেক ধরণের চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে যা আমি আড্ডায় বলতে চাই নি সে-সময়, কারণ আড্ডা তখন মধ্যরাত ছাড়িয়ে গেছে। সবাই তুহীন ঠাণ্ডা উজিয়ে ঘরে ফিরবেন। তাই আমি জানালাম আমি মাযহারের প্রবন্ধটি নিয়ে আগামী আড্ডায় কথা বলতে চাই। কিন্তু ডঃ সিদ্দিকার অভিসন্দর্ভের দুটি অধ্যায় নিয়ে আমাদের মাঝে যে আলোচনা হলো, সেবিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে যে ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আমি দুয়েকটি কথা জানালাম। জগতের বড় পণ্ডিতদের আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও অভিসন্দর্ভ পড়া আমার বহুদিনের অভ্যাস। আমি পণ্ডিত বা বড় মানুষদের চিন্তাজগতকে শনাক্ত করতে পারি এধরণের লেখা থেকে। তরুণ বয়সে সাধারণত পণ্ডিতরা অভিসন্দর্ভ লেখেন বা গবেষণা করেন। এই গবেষণার বিষয় নির্বাচন এবং অভিসন্দর্ভের বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত বা তা নির্বাচন থেকে আমি পণ্ডিতের মনের গতি প্রকৃতি ও পাণ্ডিত্যের বাইরে তাঁর মনোজগৎকে চিনতে চেষ্টা করি। ডঃ সিদ্দিকার অভিসন্দর্ভটিও আমি খুব অভিনিবেশ নিয়ে একটু সময় হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে পড়ার চেষ্টা করেছি। বিষয়টি সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও কথাশিল্পের বিভাজন রেখার মাঝামাঝি জায়গার। বিষয়টি সম্পর্কে ভাবনাকে যদি অতি উচ্চ জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যায় জ্ঞান বা শিল্পের এই তিনটি ডিসিপ্লিন প্রায় এক শীর্ষবিন্দুর কাছাকাছি এসে যায়, তাদের বিভাজন রেখা প্রায় অদৃশ্য হয়ে প্রায় ‘দর্শনের’ সীমানা-ঘেঁষা ভূখণ্ডে পৌঁছে যায়।
আমি নিজে সাহিত্য এবং ইতিহাসকে যেভাবে দেখার চেষ্টা করি, তা মনে রেখেই আমি ডঃ সিদ্দিকার অভিসন্দর্ভটি নিয়ে কথা বলতে চাই। আমি মনে করি ইতিহাস একটি বিশেষ শৃঙ্খলায় বা ডিসিপ্লিনে আবদ্ধ নয়, বরং তা মানব সমাজের বিবিধ গল্পের মাঝে ডুবে থাকে, সে-সব ‘গল্পের’ কিছু বেঁচে থাকে বইয়ের পাতায়, কিছু মানুষের মনে, আর অধিকাংশই মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়! কিন্তু সেই স্মৃতি’ সম্পূর্ণ হারিয়েও আবার যায় না। বার বার তা পুনরুল্লিখিত হয় ভিন্ন শৃঙ্খলার লেখায়, ইতিহাস আঁকা হয় শিল্পে, কবিতায়, এমনকি সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বে। যখন বিভিন্ন ‘ভাষায়’, মানে তুলিতে, কলমে বা সুরে ও মঞ্চে তা চিত্রিত হতে থাকে, তখন এই শিল্পীরা বা সমাজবিজ্ঞানীরা ইতিহাসকে কীভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, ভাবেন বা কীভাবে মহাকালের বেদিতে রেখে যেতে চান! তাঁরা যেভাবে ইতিহাস ‘পারসিভ’ করেন তা ফর্মাল ইতিহাসবিদদের থেকে অনেকটাই আলাদা। তাই ‘দেশভাগ’ নিয়ে রমিলা থাপার, রণজিৎ গুহ বা অমলেশ ত্রিপাঠী যেভাবে লেখেন, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা চিত্র আঁকেন পরিতোষ সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, বা মৃণাল সেন বা ঋত্বিক ঘটক তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পমাধ্যমে! তাহলে ভিন্ন ভিন্ন এই শিল্পীদের কাছে ‘ইতিহাস’ কী একই বিষয় হয়ে একইভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে ইতিহাসের নামে! কোনভাবে কি এই মহৎ শিল্পীরা ‘ইতিহাসের’ পুনর্নির্মাণ করেছেন তাঁদের ভিন্ন মাধ্যমে, নাকি তাঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ‘দর্শনের’ দৃষ্টি নিয়ে মহাকালের সামনে নথিবদ্ধ করে গেলেন একই বিষয়ের ‘ভিন্নতর সত্যকে’, যা কিনা সত্যের চেয়েও অধিক, ‘সত্যতর’ হয়ে ওঠে সময়ের দীর্ঘ পরিসরে! সম্ভবত এই ‘সত্যতর’কেই অন্বেষণ করে গেছেন ডঃ ফারজানা সিদ্দিকা তাঁর প্রায় সাড়ে তিনশত পাতার অভিসন্দর্ভটিতে, যা পাঠককে শুধু নতুন ‘ইতিহাসের’ দিকে নিয়ে যায় তাই নয়, তাদেরকে ইতিহাসের অংশভাক হতেও শেখায় কিছুটা। অভিসন্দর্ভটি আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে, হয়তো কথাশিল্পকে ভিন্নভাবে পড়তেও শিখিয়েছে কিছুটা!
রাত গভীর হয়েছে, সবাই বাড়ির দিকে ফিরে গেলেন! আমি নিজের কাজের টেবিলে বসলাম ফেলে রাখা কাজগুলো নিয়ে!